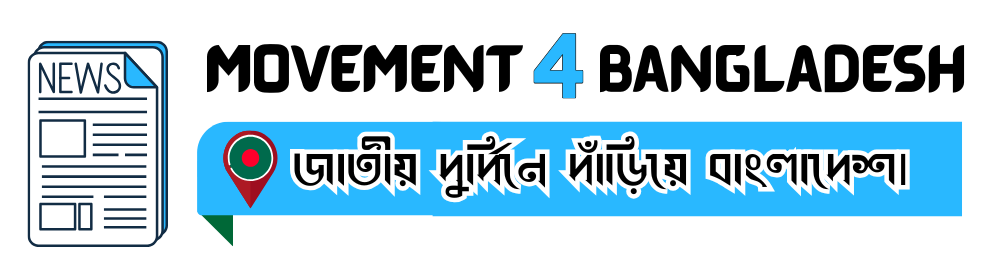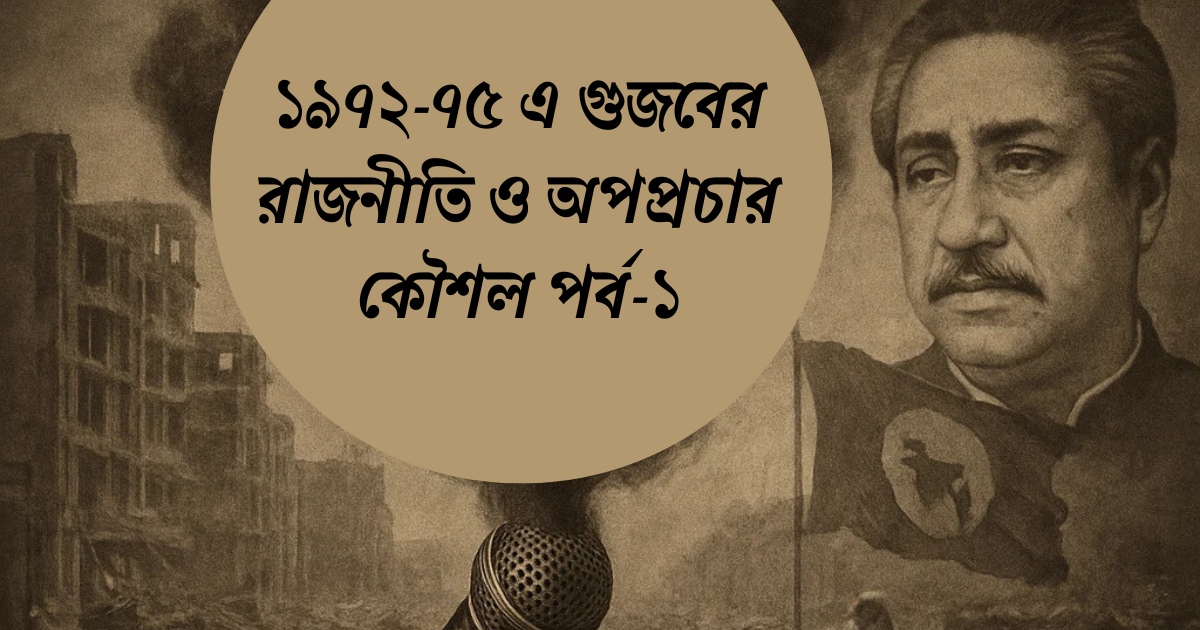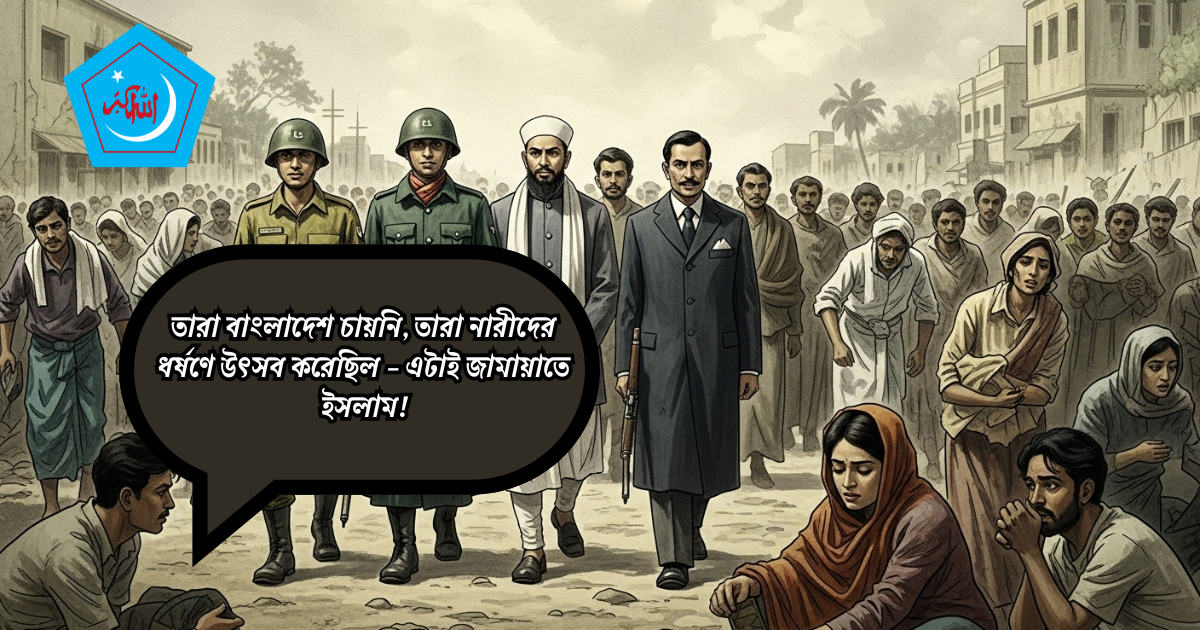বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পরপরই শুরু হয় একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্র গঠনের কঠিন যাত্রা। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ সময়েই রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয় নানামুখী গুজব, অপপ্রচার এবং রাজনৈতিক বিভ্রান্তি দ্বারা। এসব ঘটনাবলী শুধু ইতিহাসের দলিল নয়, বরং বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য এক গভীর শিক্ষা। বিশেষ করে তৎকালীন বিরোধী রাজনৈতিক দল জাসদ,ভাসানীর ন্যাপ, সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টিসহ কিছু রাজনৈতিক দল এবং গোষ্ঠী দায়িত্বজ্ঞানহীন বক্তব্য ও তথ্যবিকৃতির মাধ্যমে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করেছিল, তা জাতীয় ঐক্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এর প্রভাব শুধু অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সীমাবদ্ধ ছিল না—আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও বাংলাদেশের ভাবমূর্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। ফলে বিদেশি সহায়তা, কূটনৈতিক সম্পর্ক ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার গতি ব্যাহত হয়। এসব বিভ্রান্তিকর প্রচারণা জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করে এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল নাড়া দেয়। চলুন সেই সময় গুজব,অপপ্রচার সম্পর্কে পর্যালোচনা করি :
* ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে, আর বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কিছু রাজনৈতিক নেতার মনোভাব ছিল বিরোধিতামূলক। ১৯৭২ সালের শুরু থেকেই মোহাম্মদ তোয়াহা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করেন। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময় এঁরা বিরোধিতা করেছিলেন, তারপরও কমরেড আবদুল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, দেবেন সিকদার, সিরাজ সিকদার কিংবা আবদুল মতিনের মতো নেতাদের রাজনীতি স্বাধীন বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ছিল না।১৯৭২ সালের ৫ মার্চ, ইংরেজি সাপ্তাহিক হলিডে পত্রিকায় মোহাম্মদ তোয়াহার একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। সেখানে তিনি বলেন—
“পূর্ব বাংলা আজ বাংলাদেশ নামে ভারতের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন ক্ষমতাসীন শ্রেণীর একটি অংশের সামরিক হস্তক্ষেপ ও সহযোগিতায়।”
এই বক্তব্যের পর তোয়াহা ও তাঁর সমর্থকরা আত্মগোপনে চলে যান। চমকপ্রদ বিষয় হলো, এই আত্মগোপনের সময় মোহাম্মদ তোয়াহা কয়েকদিন লুকিয়ে ছিলেন খোদ বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেই। অথচ পরবর্তী সময়ে তিনিই বঙ্গবন্ধুকে ‘একনায়ক’ বা ‘স্বৈরশাসক’ বলে সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। যে সময়টিতে ভারত বাংলাদেশকে সবরকম সাহায্য করছিল, ঠিক তখনই এই ধরনের বক্তব্য বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক। তাছাড়া তোয়াহার বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আত্মগোপন করেও পরে তাঁকেই ‘স্বৈরশাসক’ বলার ঘটনা রাজনৈতিক সুবিধাবাদিতার এক চূড়ান্ত উদাহরণ।আজকে সেই একই মতাদর্শের উত্তরসূরিরাই নানা মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ‘বিরোধী মত দমন’-এর অভিযোগ তোলে—যা ইতিহাসের পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়।
* মওলানা ভাসানীকে ঘিরে চীনপন্থী রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো সীমিত পরিসরে হিন্দু ও ভারতবিরোধী আবেগকে উসকে দিয়ে কিছু ফায়দা তুলেছিল। এর ফলে পাকিস্তানপন্থী সাম্প্রদায়িক দলগুলো—যেমন জামাত, নিজাম, মুসলিম লীগ, আল-বদর, পিডিপি—যাদের অনুসারীরা এখনও দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিল, তারা নিজেদের অবস্থান দৃশ্যমান করার কিছুটা সুযোগ পেয়েছিল।
কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মণি সিংহ এই অবস্থাকে “পাক দালালদের ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ” বলে চিহ্নিত করেছিলেন। তবে এসব সমালোচনার মাঝেও মওলানা ভাসানী ভারতবিরোধী রাজনীতি থেকে কখনও সরে আসেননি। তিনি সময় ও প্রেক্ষাপটে এর মাত্রা বাড়িয়েছেন, কমিয়েছেন, আবার কখনো প্রকাশ্যে অস্বীকারও করেছেন—কিন্তু মূল অবস্থান অপরিবর্তিত থেকেছে। একটি ঘটনার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল, ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী কিছু ‘মাড়োয়ারি’ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ তোলেন। এর মাধ্যমে তিনি পরোক্ষভাবে ভারত ও ভারতীয় জনগণের প্রতি কঠোর সমালোচনা করেন—এমনটি রিপোর্ট করে পত্রিকা পর্বদেশ।
কিন্তু দুদিন পর ন্যাপ (ভাসানী) এই প্রতিবেদনের প্রতিবাদ জানায়। দলটির ঢাকা শহর কমিটির আহ্বায়ক মুজিবর রহমান চিশতী এবং ময়মনসিংহ জেলার সদস্য তারিকুল ইসলাম একটি যৌথ বিবৃতিতে বলেন, মওলানা ভাসানী কখনো ভারতীয় জনগণের বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ মন্তব্য করেননি। অথচ মাড়োয়ারি’ শব্দটি দিয়ে ভাসানী ও জাসদ ভারতীয় জনগণকে নয়, বরং ভারতীয় অর্থনীতিকে টার্গেট করার ভান করে ধর্মীয় ও জাতিগত বিদ্বেষ উসকে দিয়েছিল।
‘মাড়োয়ারি’ শব্দটির তখনকার রাজনীতিতে বিশেষ তাৎপর্য ছিল। শুধু ভাসানী নন, জাসদও তাদের রাজনীতিতে এই শব্দটি ব্যবহার করে। ১৯৭২ সালের ১৯ নভেম্বর, খুলনার শহীদ হাদিস পার্কে এক জনসভায় জাসদের আহ্বায়ক আ স ম আবদুর রব বলেন—”মাড়োয়ারিরা শোষণ করছে।”
* মওলানা ভাসানী ও তার দল (ন্যাপ), এমনকি পরবর্তীতে জাসদ, স্বাধীনতার পর ভারতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলতে থাকে। কিন্তু এসব অভিযোগে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ ছিল না। একদিকে বলা হতো—ভারতের ব্যবসায়ীরা, বিশেষ করে মাড়োয়ারিরা, নিম্নমানের পণ্য বাংলাদেশে বিক্রি করছে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে—এই পণ্য বাংলাদেশে আনল কে? যদি বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এগুলো আমদানি না করতেন, তাহলে ভারতীয় পণ্য আসতোই না। তাই দোষ দেওয়ার আগে নিজেদেরও দেখতে হয়। ১৯৭৪ সালে জাসদের মুখপত্র “গণকণ্ঠ” পত্রিকায় একটি খবর ছাপা হয়, যাতে বলা হয়—ভারত উড়িষ্যায় পাটকল বানাচ্ছে, অথচ সেখানে নাকি পাটই হয় না। আসলে এটা ছিল ব্যঙ্গ করে বলা, যেন বোঝায়—ভারত বাংলাদেশের পাট চুরি করে নিজ দেশে কল-কারখানা বানাচ্ছে। অথচ বাস্তবে উড়িষ্যা ও ত্রিপুরায় অল্প হলেও পাট উৎপাদন হয়।
কেন্দ্রীয় সরকার নতুন অঞ্চল থেকে উৎপাদন বাড়িয়ে রপ্তানিমুখী শিল্প গড়তে চেয়েছিল। জাসদ এই তথ্য জেনেও বিভ্রান্তিকর শব্দচয়নে এই ধরণের কথা বলেছিল, উদ্দেশ্য ছিল জনমনে ভারতবিরোধী মনোভাব তৈরি করা। এই তথ্য বিকৃতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। বাস্তব সত্য জেনেও উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকৃত তথ্য পরিবেশন প্রমাণ করে যে এটা শুধুই জনমত গঠনের একটি অপকৌশল ছাড়া আর কী হতে পারে?
* ভাসানীও পরে আরও কঠিন ভারতবিরোধী বক্তব্য দেন, কিন্তু তখন প্রতিবাদও করেন না। সম্ভবত সে সময় (১৯৭২ সালের শুরুতে) ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তাই তিনি তখন এতটা খোলাখুলি কিছু বলেননি। পরে অবশ্য তার দল ভারতবিরোধিতা স্পষ্টভাবে সামনে নিয়ে আসে।
এই ভারতবিরোধী রাজনীতিকে সমর্থন করেছিল “হলিডে” পত্রিকাও। আর সিপিবি (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি) তখন বলেছিল—ভাসানীর এই উস্কানিমূলক রাজনীতি আসলে সিআইএ (মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা)-এর ইন্ধনে চালানো হচ্ছে।
* মওলানা ভাসানী গুজব ছড়ানো এবং ভারতবিরোধিতার সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়গুলোকে মিলিয়ে অনেক সময় জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করতেন। ১৯৭২ সালের ৩ অক্টোবর হবিগঞ্জে এক জনসভায় তিনি বলেন, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং ভারত (যাকে তিনি “হিন্দুস্থান” বলে উল্লেখ করেন) বাজে পণ্য দিয়ে বাংলাদেশের বাজার দখল করছে।
কিন্তু বাস্তবে, সরকার কখনো মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার কথা বলেনি। উল্টো তারা জানিয়েছিল—মাদ্রাসা শিক্ষা বিলোপ তাদের নীতি নয়।
আর বাজার দখলের প্রসঙ্গও ঠিক নয়, কারণ যুদ্ধের পরে বাংলাদেশে নিজস্ব উৎপাদন ছিল না বললেই চলে—বিদেশি সাহায্যের ওপরেই চলছিল দেশ। তাহলে প্রশ্ন আসে—ভাসানী কিসের ভিত্তিতে ভারতের পণ্যকে “বাজে” বললেন?
“মওলানা ভাসানী ভারতীয় পণ্যকে ‘অত্যন্ত বাজে জিনিস’ বলে অভিহিত করলেও, তিনি সেই মূল্যায়নের পেছনে কোনো বাস্তব বা পরীক্ষিত মানদণ্ডের উল্লেখ করেননি। ফলে প্রশ্ন জাগে—তিনি ঠিক কোন ভিত্তিতে এসব পণ্যের গুণগত মান নির্ধারণ করেছিলেন?কী কী মানদণ্ডে বিচার করে এমন মন্তব্য করা হয়েছে? পরীক্ষিত বৈজ্ঞানিক বা কারিগরি মানদণ্ডে?
একটি স্বাধীন দেশের জনগণের বাজার ব্যবস্থার বিষয়ে এমন মন্তব্য তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন তা নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ, কারিগরি প্রতিবেদন বা ভোক্তার অভিজ্ঞতার আলোকে উপস্থাপিত হয়। অথচ, ভাসানীর বক্তব্যে আমরা এমন কোনো বিশ্লেষণ পাই না,প্রমাণও পাই না। আনিত অভিযোগের প্রমাণিত করতে পারেনি প্রমাণের ভিত্তিতে।
বরং এটি একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভারতবিরোধী মনোভাব থেকেই উদ্ভূত বলেই প্রতীয়মান হয়।”
আসলে, এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ধর্মীয় আবেগকে জাগিয়ে তুলে ভারতবিরোধী মনোভাব গড়ে তোলা এবং ন্যাপের সাম্প্রদায়িক সমর্থকদের খুশি করা।
এই ভারতবিরোধিতার মোড়কে ভাসানী ধর্মীয় রাজনীতিকে সামনে আনতে চেয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালের ৭ জানুয়ারি, তিনি এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শপথ নিয়েছিলেন “জেহাদে” নামার, যার লক্ষ্য শুধু ভারত নয়, বরং বাংলাদেশের সেই সব মানুষ, যারা ধর্মীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি নষ্ট করতে চায়—এমন দাবি ছিল তার। তিনি বলেন, দেশের ৮৬ শতাংশ মুসলমানের শত্রুদের বিরুদ্ধে এই জেহাদ হবে।
এই ধরনের বক্তব্যে স্পষ্টভাবে দেখা যায়, ভাসানীর রাজনীতি কেবল ভারতবিরোধী ছিল না, বরং তা ছিল সাম্প্রদায়িক। তিনি ধর্মীয় বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান আমলের মতো ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে নতুন করে জায়গা করে দিতে চাইছিলেন।
এখানে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ:
ভারতের নাম “হিন্দুস্থান” নয়, “ভারত”—এমন শব্দ ব্যবহার ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি ছড়ায়।
কোনো প্রতিবাদ যদি হয়, তা নাগরিক পরিচয়ে হওয়া উচিত, ধর্মীয় পরিচয়ে নয়। শুধু মুসলমানদের পক্ষে প্রতিবাদ মানেই তা একপেশে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে যায়।
স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুতেই মওলানা ভাসানী ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করেন। পাকিস্তান আমলে যেমন সামরিক সরকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করে জনগণকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিল, তেমনিভাবে ভাসানীও ১৯৭২ সালে মসজিদে খুৎবা ও পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাব ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি
“বাংলা খুৎবা” নামে একটি বই বের করেন, যেখানে ধর্মীয় বক্তব্যের আড়ালে ভারতের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো হয়েছিল।
তিনি মসজিদের মিম্বর থেকে জনগণকে আহ্বান জানান—“হিন্দুস্থানের দাসত্ব ঝেড়ে ফেলো”, যা এক ধরনের সাম্প্রদায়িক উসকানি। তখনো বাংলাদেশের স্বাধীনতার এক বছর হয়নি; দেশটি ছিল আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সহানুভূতির ওপর নির্ভরশীল। ঠিক সেই সময়ে এমন উসকানিমূলক বক্তব্য দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এবং আন্তর্জাতিক সাহায্যও বাধাগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করে। তবে বাংলাদেশের মানুষ তখন এতটা বিভ্রান্ত ছিল না। সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্রে সাধারণ জনগণই প্রশ্ন তুলেছিল—এই ধরনের কথা কি সত্যি ‘বাকস্বাধীনতা’, নাকি স্রেফ গুজব ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপপ্রচার?
শুধু ভাসানী নন, আতাউর রহমান খানের বাংলা জাতীয় লীগও একইরকম ভারতবিরোধী কথাবার্তা বলেছিল। তারা বলেছিল, “পাকিস্তানের হাত থেকে মুক্তি পেলেও এখন বাংলাদেশ দিল্লীর দাসত্বে পরিণত হয়েছে।” অর্থাৎ একই ধরনের বক্তব্যকে শুধু ভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।
এছাড়া, ১৯৭৪ সালে হলিডে পত্রিকায় একটি ভুয়া রিপোর্ট ছাপা হয়, যেখানে বলা হয়—শেখ মুজিব ও তার পরিবারের নামে সুইস ব্যাংকে প্রচুর অর্থ জমা আছে। সরকারের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলে জানা যায়—এই তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং এর কোনো প্রমাণ নেই এবং পরবর্তী সরকার এলেও তার প্রমাণ বের করতে পারেনি । তবু ওই সংবাদ প্রকাশের দায়ে সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খানের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। “হলিডে পত্রিকায় শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারকে নিয়ে ভুয়া খবর প্রকাশের ঘটনায় তদন্ত কমিটি সম্পাদক এনায়েতউল্লাহ খানের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তিনি পরে ক্ষমা চেয়ে শেখ ফজলুল হক মনির সাহায্য নেন এবং শেষ পর্যন্ত কোনো শাস্তি হয়নি। ফলে সরকারের গাফিলতিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।”
* ১৯৭৩ সালের ৩ জানুয়ারি, ‘ভিয়েতনাম সংহতি দিবস’ উপলক্ষে বায়তুল মোকাররমে আয়োজিত এক সমাবেশে জাসদের সাধারণ সম্পাদক আ স ম আবদুর রব ঘোষণা দেন:
“বাংলাদেশের মাটিতে কোনো মার্কিন দূতাবাস থাকতে পারবে না এবং ভিয়েতনামের বদলা বাংলাদেশে নেওয়া হবে।”
এই বক্তব্য আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এক দেশের বিরুদ্ধে অন্য দেশে প্রতিশোধ নেওয়ার চিন্তা কেবল রাজনৈতিক অবিবেচনার পরিচয় নয়, এটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের নীতিগত অবস্থানকেও দুর্বল করে।
*জাসদ ছিল মূলত তরুণ নেতৃত্বনির্ভর একটি দল, যারা তথাকথিত ‘গোপন তথ্য’ বা ‘অভ্যন্তরীণ খবর’ দিয়ে জনমনে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিল। এর ফলে দেশীয় রাজনীতির গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক মহলেও এই গুজব আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারিতে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে আ স ম আবদুর রব বলেন:
“আমি শুনেছি”, “আমাদের কাছে খবর আছে…”
এই ধরনের অস্পষ্ট সূত্রের ভিত্তিতে তিনি অভিযোগ করেন:
১.চট্টগ্রাম বন্দর ও বঙ্গোপসাগরে বিদেশি সৈন্য মোতায়েন রয়েছে।
২.রক্ষীবাহিনীতে বিপুলসংখ্যক ভারতীয় সৈন্য কাজ করছে।
এমন অভিযোগ দায়িত্বশীল রাজনৈতিক নেতার জন্য যেমন অনুচিত, তেমনি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্যও হুমকিস্বরূপ। এগুলোর কোনো প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি এবং পরে সেগুলো ভিত্তিহীন বলেই প্রমাণিত হয়েছে।
* ১৯৭৩ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত জাসদের জাতীয় কমিটির সভায় কিছু চাঞ্চল্যকর এবং অতিরঞ্জিত দাবি উপস্থাপন করা হয়, যার দুটি প্রধান ছিল:
1. “স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে আসা সাহায্য সামগ্রী সশস্ত্র সংগ্রামে ধ্বংসের পরিমাণের চেয়েও বেশি।”
2. “গত দুই বছরে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মী ও মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার সংখ্যা ১৯৭১ সালের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যার চেয়েও বেশি।”
এই দুই দাবিই বাস্তবতা ও পরিসংখ্যানগত সত্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলেই প্রতীয়মান হয়।
প্রথম দাবি ছিল, বাংলাদেশে আসা বিদেশি সাহায্য সশস্ত্র সংগ্রামে যে ক্ষতি হয়েছিল, তার চেয়েও বেশি। এই বক্তব্য বাস্তবতা থেকে দূরে, কারণ:
১৯৭২ সালে জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, কেবল অবকাঠামোতে পাকিস্তানি বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পরিমাণ ছিল প্রায় ৯,৬০০ মিলিয়ন টাকা (১.২ বিলিয়ন ডলার), যা তৎকালীন বাংলাদেশের মোট জিডিপির ২১% এরও বেশি।
অর্থাৎ যুদ্ধকালে ধ্বংসের পরিমাণ ছিল বিশাল ও ব্যাপক — যা শুধু রাস্তাঘাট বা ব্রিজ নয়, বিদ্যুৎকেন্দ্র, রেললাইন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি একত্রে ধ্বংস করেছিল।
এ প্রেক্ষাপটে, ১৯৭২-৭৩ সালের বিদেশি সাহায্যের পরিমাণ কখনোই এই ধ্বংসপ্রবণতার সমান বা বেশি ছিল না। ফলে, জাসদের বক্তব্যটি ছিল সংখ্যাগতভাবে ভুল ও যুক্তিহীন।
দ্বিতীয় দাবিটি — যে স্বাধীনতার পর দু’বছরে মুক্তিযোদ্ধা ও বিরোধীদলীয় নেতাদের হত্যার সংখ্যা ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যার চেয়েও বেশি — তা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও শহিদদের সংখ্যার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।
স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ শহিদ হন বলে সাধারণভাবে অনুমান করা হয়, যদিও গবেষণাভিত্তিক সংখ্যাও লক্ষাধিক।
আর শুধুমাত্র সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা হিসেব করলেও হাজার হাজার ব্যক্তি সরাসরি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছেন।
অথচ, ১৯৭২-৭৩ সালে বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে সহিংসতার কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটলেও তা সংখ্যায় বা প্রক্রিয়াগতভাবে কোনোভাবেই ১৯৭১-এর গণহত্যার সঙ্গে তুলনীয় নয়। অতএব, জাসদের এই দাবি ছিল ইতিহাস বিকৃতি ও রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির প্রয়াস। মনে রাখতে হবে,আন্তর্জাতিক কোনো মানবাধিকার সংস্থা বা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানও এই দাবিকে সমর্থন করে এমন তথ্য প্রকাশ করেনি যে যার ভিত্তিতে তারা এই ধরণের কথা বলবে।
প্রিয় পাঠক আপনাদের কাছে দুটো প্রশ্ন রাখতে চাই :
১. তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ কতটুকু ছিল?
১৯৭০-এর দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশে স্বাধীন গণমাধ্যম, তথ্যপ্রযুক্তি বা শক্তিশালী গবেষণা প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে গড়ে ওঠেনি। সরকারের তথ্য সরবরাহ ছিল সীমিত এবং বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রচারব্যবস্থা একমুখী ছিল। ফলে সাধারণ মানুষের জন্য গুজবের সত্যতা যাচাই করা ছিল প্রায় অসম্ভব।
২. আওয়ামী লীগ সরকার না থাকাকালে, আদালত বা বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে এসব গুজবের সত্যতা যাচাই কি সম্ভব হয়েছিল?
বাস্তবতা হলো, বিচারব্যবস্থা তখনও স্বাধীনভাবে কাজ করার মতো কাঠামো ও রাজনৈতিক পরিবেশ পায়নি। অতিপ্রচারিত বা মিথ্যা রাজনৈতিক বক্তব্য আদালতের মাধ্যমে যাচাই করার সুযোগ ছিল সীমিত থেকে নিষ্ক্রিয় পর্যায়ে। বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলো যখন ক্ষমতার বাইরে ছিল, তখন অনেক সময় বিচার ব্যবস্থাও ছিল নানা চাপ ও প্রভাবের মধ্যে।
…চলবে..
তথ্যসূত্র :
তথ্যসূত্রঃ তথ্যসূত্র :
গ্রন্থ
১. আহমদ, মহিউদ্দিন। (২০২০)। বেলা-অবেলা: বাংলাদেশ ১৯৭২-১৯৭৫। বাতিঘর।
২. তোয়াহা, মোহাম্মদ। (২০১৬)। স্মৃতিকথা। সংস্কৃতি প্রকাশনী।
৩.রসূল, মারুফ। বাকশালের আদ্যোপান্ত, পৃষ্ঠা ৬৫–৭০। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।
৪. ভাসানী, মওলানা আবদুল হামিদ খান। (১৯৭২)। বাংলা খুতবা।
১৯৭২-৭৫ সমসাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্র,দলীলপত্র :
১. আজাদ। (১৯৭২, ৮ অক্টোবর)। মাওলানা ভাসানী বলেন: মাদ্রাসা শিক্ষার নিশ্চয়তা চাই, পৃ. ৫।
২. আজাদ। (১৯৭২, ৩ নভেম্বর)। অন্তরঙ্গ বর্ণনা, উপ-সম্পাদকীয়, পৃ. ৪।
৩. আজাদ। (১৯৭২, ২৯ নভেম্বর)। রায়, শ্রী নৃপেন্দ্রনাথ। ভাসানী সাহেব জবাব দিন, চিঠিপত্র, পৃ. ৪।
৪. আজাদ। (১৯৭৩, ১১ জুন)। মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে পাক দালালরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে: কমিউনিস্ট নেতা মনি সিং, পৃ. ১, ৭।
৫. বাংলা। (১৯৭২, ৮ সেপ্টেম্বর)। মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা বিলোপ সরকারের নীতি নয়, পৃ. ৩।
৬. বাংলাদেশ অবজারভার। (১৯৭২, ১৬ নভেম্বর)। ভাসানী ব্যাক টু পলিটিক্স অফ কমিউনালিজম, পৃ. ১, ৮।
৭. দৈনিক গণকণ্ঠ। (১৯৭৪, ১ জানুয়ারি)। ভারতে আরও একটি পাটকল নির্মিত হচ্ছে, পৃ. ১, শেষ।
৮ . দৈনিক ইত্তেফাক। (১৯৭২, ৯ অক্টোবর)। চতুরঙ্গ, উপ-সম্পাদকীয়, পৃ. ২।
৯ . দৈনিক ইত্তেফাক। (১৯৭৪, ৯ জানুয়ারি)। মাওলানা ভাসানীর দুর্বার ‘জেহাদ’ শুরুর শপথ, পৃ. ১, শেষ।
১০ . দৈনিক পূর্বদেশ। (১৯৭২, ১০ এপ্রিল)। অন্যান্য দলের প্রতি ভাসানীর কটাক্ষ, পৃ. ১, শেষ।
১১. দৈনিক পূর্বদেশ। (১৯৭২, ১২ এপ্রিল)। পূর্বদেশে প্রকাশিত মাওলানা ভাসানীর পল্টন জনসভার রিপোর্ট প্রসঙ্গে, পৃ. ১, শেষ।
১২. দৈনিক পূর্বদেশ। (১৯৭২, ২০ অক্টোবর)। সামাদ, ড. এবনে গোলাম। ভাসানী কি চান: খাদ্য না যুদ্ধ, উপ-সম্পাদকীয়, পৃ. ৪।
১৩. দৈনিক সংবাদ। (১৯৭২, ২০ নভেম্বর)। মাড়োয়ারীরা শোষণ করছে: রব, শেষ পাতা।
১৪. দৈনিক সংবাদ। (১৯৭২, ৪ ফেব্রুয়ারি)। আজাদ বাংলা গড়ে তুলন: অলি আহাদ।
১৫. হলিডে। (১৯৭২, ৮ অক্টোবর)। Bhashani: The First Crusader, pp. 1, 8.
১৬. The People. (1972, October 18). Communal disharmony: CPB blames CIA and Bhashani, pp. 1, 6.
১৭. “এছলামই মানব সমাজকে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে”, দৈনিক আজাদ, ০১ নভেম্বর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা ৪।